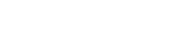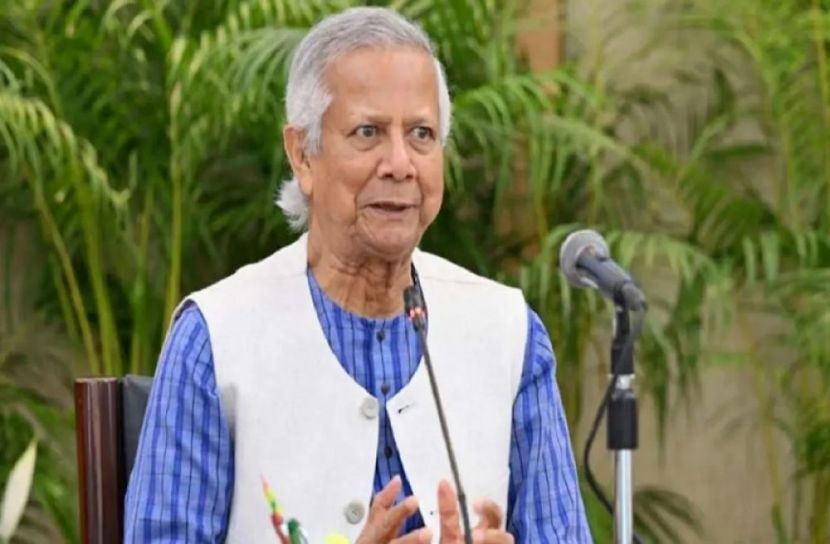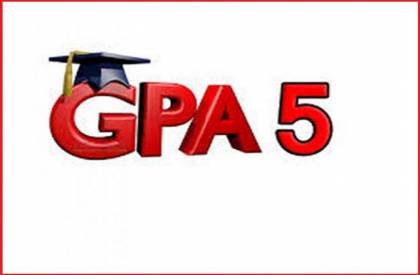আবদুল মান্নান: প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখ একাত্তর সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর জামায়াত, আল-বদর ও রাজাকারদের দ্বারা হত্যা করা বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস’ পালন করা হয়। এই বছর দিবসটি স্বাধীন বাংলাদেশে ৫১তম বার পালন করা হচ্ছে। একাত্তরে ঘাতকদের হাতে যত বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছেন, তাদের অত্যাচারে পঙ্গু হয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। যদিও একটি দিনকে একাত্তরে নিহত বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; বাস্তবে বছরের প্রতিটি দিনই যেমন গণহত্যা দিবস, ঠিক একইভাবে প্রতিটি দিনই শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। কারণ, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে বাংলাদেশে গণহত্যার শুরু থেকেই বুদ্ধিজীবী নিধন শুরু হয়েছিল, যা পুরো ৯ মাস চলেছে।
আরও পড়ুন: একাত্তরের পরাজিতরা ফের সক্রিয় হচ্ছে
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনও হঠাৎ চিন্তার ফসল নয়। এর পেছনে আছে দীর্ঘদিনের চিন্তা ও প্রস্তুতি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামের বিকলাঙ্গ রাষ্ট্রটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল পূর্ব বাংলার বাঙালিরা, যাদের মধ্যে সব সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। মুসলিম লীগ নেতারা যে ইকবালকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন, সেই ইকবালের স্বপ্নের পাকিস্তানে কখনও বাংলার অস্তিত্ব ছিল না। আসলে ইকবাল কখনও পাকিস্তান চাননি। তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতের অবহেলিত মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধা সংবলিত এক সংরক্ষিত অঞ্চল চেয়েছিলেন।
১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামীর ইন্ধনে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে কাদিয়ানিবিরোধী এক দাঙ্গা হয়। তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন। দাঙ্গা প্রশমিত করতে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে জেনারেল আজম খানকে (পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় গভর্নর) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ঘটনা তদন্ত করতে সরকার বিচারপতি মোহাম্মদ মুনিরকে (পরে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি) দিয়ে একটি দুই সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। অন্য সদস্য ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ রুস্তম কায়ানি (পরে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি)।
আরও পড়ুন: বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা
তাঁরা ঘটনা তদন্তপূর্বক যে দীর্ঘ প্রতিবেদন দাখিল করেন তাতে উল্লেখ করেন ‘Even Dr. Muhammad Iqbal who must be considered to be the first thinker who conceived of the possibility of a consolidated North Western Indian Muslim State, in the course of his presidential address to the Muslim League said : ‘Nor should the Hindus fear that the creation of autonomous Muslim States will mean the introduction of a kind of religious rule in such states. The principle that each group is entitled to free development on its own lines is not inspired by any feeling of narrow communalism.’’
এমনকি চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হবে তা ধারণা করা হয়নি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের বিষয়টাও তেমন একটা বড় বিষয় হিসেবে দেখা হয়নি। বড়জোর একটা ফেডারেল রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের দিল্লি কনফারেন্সে প্রথমবারের মতো ঠিক করা হয় মুসলমানদের জন্য ভারতে একটি পৃথক রাষ্ট্র হবে। তা ভারত ভাগ হয়ে হবে, না ভারতকে অখণ্ড রেখে হবে তাও পরিষ্কার ছিল না। তবে এসব বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা না করেও বলা যায়, বাংলা ভাগ হয়ে একটি অংশ যে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো তা অনেকটা রাজনীতিবিদদের নির্বুদ্ধিতার ফল। অবিভক্ত বাংলাও একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারতো এবং তার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরন শঙ্কর রায়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম প্রমুখ। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, যার জন্য রাজনীতিবিদদেরই দায় নিতে হবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানের পাঞ্জাবের সামরিক-বেসামরিক শাসকগোষ্ঠী এটি উপলব্ধি করেছে, তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা যেভাবে তাদের বশ্যতা ও হুকুম তামিল করে, পূর্ব বাংলার মানুষ তা করতে অস্বীকার করেন। সেখানকার মানুষ, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ তাদের অধিকারের বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন এবং প্রয়োজনবোধে প্রতিবাদ করে, প্রতিহত করে, যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ১৯৪৮ সালে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন।
আরও পড়ুন: কঙ্গোতে বন্যা-ভূমিধসে নিহত ১২০
১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ২১ মার্চ ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের ছয় ভাগ মানুষের ভাষা উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। জিন্নাহ নিজে কিন্তু উর্দু জানতেন না। জিন্নাহর এমন অবিবেচনাপ্রসূত ঘোষণা ছিল উত্তর ভারত ও বিহার থেকে পাকিস্তানে চলে আসা মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা। পাকিস্তানের শুরুতে এই অন্যায় প্রস্তাবের প্রথম বিরোধিতা এসেছিল বাংলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ থেকে, যার মূল উৎপত্তি ঢাকায় তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া পাকিস্তানের যত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে তার সবকটিরই উৎপত্তি বাংলাদেশে এবং তা শুরু হয়েছিল মূলত বাংলার বুদ্ধিজীবীদের হাত ধরেই। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অবদান ছিল অসামান্য। তারও আগে ত্রিশের দশকের চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ, ছেচল্লিশের তেভাগা আন্দোলন, ব্রিটিশ হোক বা পাকিস্তানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এ দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ।
আরও পড়ুন: বিমানবন্দরে ট্যাংকলরিতে আগুন
একটি দেশের বা রাষ্ট্রের প্রাণ বা আত্মা হচ্ছে তার বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজ। কারণ, তাঁরা ভালো আর মন্দের মধ্যে তফাৎ বোঝেন। যুগ যুগ ধরে এই সত্য দেশে দেশে শাসকগোষ্ঠী বুঝেছে। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী প্রায় ২০০ বছর এই উপমহাদেশ শাসন ও শোষণ করেছে; কিন্তু তাদের শাসনামলের প্রথম ১০০ বছর শিক্ষাব্যবস্থা চরমভাবে অবহেলিত থেকেছে। ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকেলেকে প্রধান করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের জন্য উপযুক্ত একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেন। কাজ শেষে তিনি যে রিপোর্ট দেন তার মূল বিষয় ছিল ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হবে যে শিক্ষিত ব্যক্তিরা হবেন রক্তে-মাংসে ভারতীয়, আর চিন্তা-চেতনায় ইংরেজ। যাত্রাটা শুরু করতে হবে তাদের ‘নিম্নমানের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা’ ভুলিয়ে দিয়ে। ১৯২২ সাল পর্যন্ত ভারতীয় প্রশাসনযন্ত্র ছিল ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে। তারা কখনও চায়নি ভারতীয়রা প্রশাসনে থাকুক।
পাকিস্তানি শাসকরাও একই চিন্তাধারা পোষণ করতেন এবং যে কারণে পাকিস্তানি প্রশাসনে পাঞ্জাবিদের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। যেমনটি বলেছিলাম, বুদ্ধিজীবী বা প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন একটি আধুনিক রাষ্ট্রের আত্মা। তাঁরা ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যটা যত দ্রুত বোঝেন, অন্যরা ততটা বোঝেন না। যে কারণে তদানীন্তন পূর্ব বাংলা বা এমনকি অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন সময়ে শাসকগোষ্ঠীর যে নির্যাতন, নিপীড়ন, জেল-জুলুম নেমে এসেছে তা অন্যদের তেমন একটা ভোগ করতে হয়নি। সেটি যেমন নেতাজি সুভাষ বোসের বেলায় সত্য, ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বেলায়ও সত্য।
আরও পড়ুন: কাভার্ডভ্যান চাপায় নিহত ২
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের দিবাগত রাতে যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল তার একটা ধরন ছিল। প্রথম টার্গেট জাতি-ধর্ম-রাজনৈতিক বিশ্বাস-নির্বিশেষে সব বাঙালি নিধন। শুরুটা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা দিয়ে। তারপর বেছে বেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, তারপর ধর্মীয় সংখ্যালঘু, এরপর দেশের তরুণ সমাজ, আর সারা বছর ধরে বিভিন্ন শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দেখেছে, যেই মুহূর্তে একাত্তর সালের ১ মার্চ এক রেডিও ঘোষণার মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান গণপরিষদের আসন্ন অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন তার প্রথম প্রতিবাদটির সূচনা হয়েছিল ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। পর্যায়ক্রমে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন দেশের শিক্ষক, লেখক, শিল্পীসহ সব শ্রেণির বুদ্ধিজীবী আর তাঁদের অনুসরণ করে শ্রমিক-কৃষকরা। তাঁরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, সংগীতের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছেন, সভা-সমাবেশে গিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁদের বেশিরভাগেরই কোনও রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। তাঁরা আত্মা আর বিবেকের তাড়নায় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এটি ঠিকই জানতো, সরল জনগণকে যত সহজে বোকা বানানো যায় একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে তত সহজে বোকা বানানো সম্ভব নয়। কারণ, তাঁরা ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝেন। সেই কারণেই শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশে দখলদার শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম টার্গেট ছিল এই শিক্ষিত সমাজ ও বুদ্ধিজীবী। একাত্তরে গণহত্যা শুরু হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের হত্যার মধ্য দিয়ে এবং তা শেষ দিন পর্যন্ত চলেছে।
আরও পড়ুন: জনগণ অপশক্তিকে প্রতিরোধ করেছে
শুরুতে বুদ্ধিজীবী নিধনের কাজ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অনেকটা এককভাবে করলেও খুব দ্রুত তারা তাদের এদেশীয় দোসরদের সার্বিক সহায়তা পেয়ে যায়। চট্টগ্রামের কুন্ডেশ্বরীর স্বত্বাধিকারী নূতন চন্দ্র সিংহকে নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করেছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। একেবারে দলগতভাবে এগিয়ে এসেছিল গোলম আযম আর মতিউর রহমানের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী ও তাদের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের কিলিং স্কোয়াড আলবদর আর মুসলিম লীগের আলশামস। তাদের সার্বিকভাবে সহায়তা করে দেশভাগের পর ভারত থেকে এ দেশে আসা অবাঙালিরা। এদের সবাইকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতো পাকিস্তান সরকার। বিভিন্ন জেলায় এই আলবদর আর আলশামসরা সৃষ্টি করেছিল বধ্যভূমি।
আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে পাকিস্তানি শাসকদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় এই যুদ্ধে তাদের বিজয়ী হওয়া অনেকটা অসম্ভব, যদি না কোনও বড় ধরনের আন্তর্জাতিক শক্তি তাদের প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। সে পথও অনেকটা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কূটনীতি ও জাতিসংঘে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থানের কারণে। তত দিনে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে প্রায় সব ফ্রন্টে পর্যুদস্ত করে ফেলেছেন। নভেম্বর নাগাদ স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। তারা এই উপসংহারে উপনীত হয়, বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঠেকানো যাবে না, তবে তাদের আত্মা আর বিবেককে ধ্বংস করে দিলে দেশটা সত্যিকার অর্থে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে কখনও উঠে দাঁড়াতে পারবে না। সব সময় সবকিছুর জন্য অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। হতে পারে তা পাকিস্তানের দিকেই। তবে বর্তমানে সেই পাকিস্তান বাংলাদেশ হতে চায়। পাকিস্তান তাদের শেষ কামড়টা দিলো বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে। এইবার তাদের অন্যতম সহায়ক শক্তি জামায়াতে ইসলামী ও আলবদর।
আরও পড়ুন: বিমানবন্দরে ট্যাংকলরিতে আগুন
নীলনকশাটা তৈরি করা হয়েছে পাকিস্তানের জেনারেল রাও ফরমান আলীর হাতে। তিনিই তৈরি করতেন টার্গেটদের তালিকা। সহায়তা নিতেন স্থানীয় পাকিস্তানপন্থি নেতাদের। অনেক ক্ষেত্রে তাতে সহায়তা করতেন কিছু বুদ্ধিজীবী, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও এই সহায়তাকারীদের তালিকা থেকে বাদ যাননি। তারা কমবেশি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ ও বেগম জিয়ার শাসনামলে নানাভাবে পুরস্কৃতও হয়েছেন। কয়েকজন মন্ত্রিসভায়ও ঠাঁই পেয়েছেন।
এটি ভাগ্যের ব্যাপার, ঘাতকরা অনেক পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীর অবস্থান শনাক্ত করতে পারেননি। হয় তারা আগেই আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন অথবা দেশ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু সবার ভাগ্যে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। নিজ বাড়ি বা কর্মস্থল থেকে ঘাতকরা তুলে নিয়ে হত্যা করেছিল ডাক্তার আলিম চৌধুরী, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক নিজামউদ্দিন, লেখিকা সেলিনা পারভিনসহ অনেককে। তাঁদের বেশিরভাগকেই গুলি করে নয়, পেছনে হাত বেঁধে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়। কারও কারও চোখ উপড়ে ফেলা হয়। শেষের দিকের এই কাজটি হয় মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে । তাদের ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায় রায়ের বাজার আর মিরপুর বধ্যভূমিতে। অন্যান্য জেলাতেও এমন অসংখ্য বধ্যভূমির হদিস মিলে পরবর্তীকালে। প্রতিবছর যখন এই দিনটি আসে আমরা সবসময় রায়েরবাজার বা মিরপুরের বধ্যভূমির কথা মনে করি, অন্যগুলোর কথা তেমন একটা বলি না । বাস্তবটা হচ্ছে, সারা বাংলাদেশই একটা বধ্যভূমি।
আরও পড়ুন: মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেফতার ৩৯
স্বাধীন বাংলাদেশে জীবিত বুদ্ধিজীবীরা দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুকে নানাভাবে সাহায্য-সহায়তা করেছিলেন। পরিকল্পনা কমিশন গঠন থেকে শুরু করে সংবিধান প্রণয়ন, বিদেশে দূতাবাস চালু করা, স্বাধীন দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা আবার শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া কোনও কিছুই বাদ যায়নি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এসব বুদ্ধিজীবীর দেশের প্রতি এতই ভালোবাসা ছিল যে তাঁদের অনেকেরই নিজ দফতরে কাজ করার জন্য টেবিল-চেয়ারও ছিল না। যাতায়াতের বাহন ছিল অনেকের ক্ষেত্রে রিকশা। বেতন ছিল দেড় হাজার থেকে তিন হাজার টাকা। তাঁরা সবাই দেশ গঠনে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন।
আরও পড়ুন: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতীয় পার্টির নেতাদের সাক্ষাৎ
৫১ বছর পর চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখনও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী বা পেশাজীবী আছেন, তবে একটি বড় অংশ আছে যারা নিজের দেশের স্বার্থ বিদেশে বিকিয়ে দিতে চোখের পলক ফেলেন না, নির্দ্বিধায় নিজের দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করেন। বঙ্গবন্ধু বলতেন, ‘আমার দেশে গরিব কৃষক চুরি-দুর্নীতি করে না। দুর্নীতি করে শিক্ষিতজনেরা’। বঙ্গবন্ধুর আমলের তুলনায় দেশে এখন জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। কিন্তু তাদের অনেকের মধ্যে একাত্তরের সেসব বুদ্ধিজীবী বা পেশাজীবীর তুলনায় দেশপ্রেমের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। সরকারি কর্মকর্তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারের সব শুভ পরিকল্পনাকে বানচাল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করায় তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। আজকের এই দিনে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত সব বুদ্ধিজীবীর প্রতি রইলো আবারও সশ্রদ্ধ অভিবাদন। বিনম্র শ্রদ্ধা রইল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাঁর পরিবার, জাতীয় চার নেতা ও ৩০ লাখ শহীদের প্রতি।
লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক